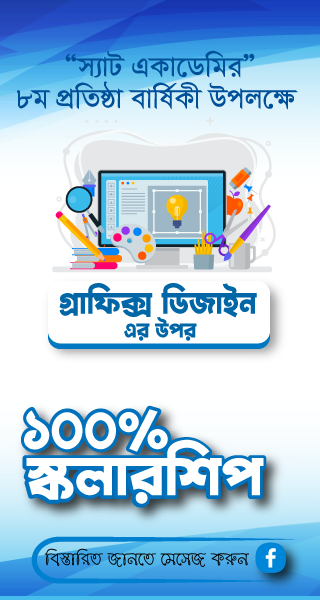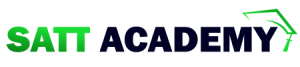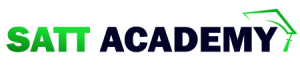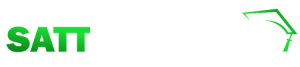একদিন নিসর্গ ও অন্বেষা তাদের বন্ধুদের সাথে গ্রামের পশ্চিম প্রান্তে বিলের ধারে ঘুরতে গেল। সেখানে হঠাৎ একটা জরাজীর্ণ স্তম্ভের মতো দেখে তাদের কৌতূহল হলো। একজন বয়স্ক মানুষকে জিজ্ঞাসা করে তারা জানতে পারলো ওটা আসলো একটা বধ্যভূমি। এই এলাকায় একসময় একটা যুদ্ধ হয়েছিল। তখন নাকি অনেক মানুষকে কারা এখানে হত্যা করেছিলো। সেজন্যই এই জায়গাটার নাম বধ্যভূমি। তাদের স্মৃতি ধরে রাখার জন্যই এই স্তম্ভ তৈরি করা হয়েছিল। এখন আর এটার কথা কেউ তেমন মনে করে না। যত্নের অভাবে এটা হারিয়ে যেতে বসেছে। ফেরার পথে সবাই বেশ চুপচুপ হয়ে থাকলো। কবে কখন যুদ্ধ হয়েছিলো? কাদের সাথে যুদ্ধ হয়েছিল? কেনই বা যুদ্ধ হয়েছিল? মানুষগুলোকে কেনই বা হত্যা করা হলো এই সব প্রশ্ন তাদের আচ্ছন্ন করে রাখলো সারাক্ষন।
মুক্তিযুদ্ধকে আমরা জানতে চাই
পরদিন স্কুলে ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান ক্লাসে খুশি আপাকে পেয়ে তারা সবাই একসাথে অনেক প্রশ্ন করতে শুরু করলো। খুশি আপা একটু থেমে বললেন, থামো থামো! আমাকে বুঝতে দাও আগে। তার মানে তোমরা আমাদের গ্রামের পশ্চিম প্রান্তে বিলের ধারে মুক্তিযুদ্ধের সময়কার যে বধ্যভূমি আছে সেখানে। দিয়েছিলে। খুব ভালো একটা কাজ করেছ তোমরা। আচ্ছা, তোমরা তো জানো যে, ১৯৭১ সালে আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধ হয়েছিল পাকিস্তানিদের সাথে। তোমাদের প্রশ্নগুলো শুনে মনে হচ্ছে তোমরা আমাদের এলাকায় মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে জানতে চাচ্ছো। কিন্তু কীভাবে আমরা এ বিষয়ে জানতে পারি বলো তো?
নিসর্গ ও অন্বেষার বন্ধু স্বাধীন বলে উঠলো, কীভাবে আর, অনুসন্ধানী কাজের মাধ্যমে।
খুশি আপা বললেন যে, চমৎকার। তাহলে চলো আমরা একটি অনুসন্ধানমূলক প্রকল্পভিত্তিক কাজের মাধ্যমে। এ সম্পর্কে জানার চেষ্টা করি।
জয় বললো, অনুসন্ধানমূলক কাজ তো আমরা জানি। কিন্তু প্রকল্পভিত্তিক কাজটা আবার কী?
খুশি আপা বললেন, তোমাদের কি ক্লাব কার্যক্রম বিষয়ক আলোচনায় শ্যামলী গল্পের (পু....) কথা মনে আছে? চলো আমরা নিচের প্রশ্নগুলো অনুসরণ করে "শ্যামলী" গল্পে শিক্ষার্থীরা যে পদ্ধতিতে কাজ করেছে তার যেসব ফলাফল পেয়েছিল সেসব আরেকবার পড়ে নেই।
কাজ শেষে জয় বললো, খেয়াল করেছো, গল্পের শিক্ষার্থীরা প্রথমে সমস্যা চিহ্নিত করেছে, তারপর অনুসন্ধানের ধাপ অনুসরণ করে প্রশ্নের উত্তর বা সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করেছে। কাজটি করতে তাদের তুলনামূলকভাবে দীর্ঘ সময় লেগেছে। গ্রামবাসী ও বনের পশুপাখিরা এ উদ্যোগের ফলে সরাসরি উপকৃত হয়েছে।
| প্রকল্পভিত্তিক কাজে মূলত সক্রিয় অনুসন্ধানের মাধ্যমে আমরা কোনো বাস্তব সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করি অথবা কোনো চ্যালেঞ্জিং প্রশ্নের উত্তর খুঁজি। সাধারণত এই কাজগুলো তুলনামূলকভাবে দীর্ঘসময় ধরে করে থাকি। অনুসন্ধানমূলক কাজের মাধ্যমে আমরা যে ফলাফল পাই তা সমস্যাটির সাথে সংশ্লিষ্ট মানুষের কাছে উপস্থাপন করি যাতে তারা উপকৃত হতে পারে। |
মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে আলোচনা
সমস্যা চিহ্নিতকরণ/অনুসন্ধানের জন্য প্রশ্ন
এরপর খুশি আপা বললেন, এবার এসো আমরা আমাদের সবার আগ্রহের বিষয় মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে ভাবি। সবাইকে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক কিছু প্রশ্ন করলেন, যার কিছু আমাদের জানা, কিছু অজানা। তিনি বললেন,
তোমরা কি জানো-
ক) আমাদের দেশ কীভাবে স্বাধীনতা পেয়েছে?
খ) কেনো মুক্তিযুদ্ধ হয়েছে?
গ) কখন এবং কত দিন ধরে মুক্তিযুদ্ধ হয়েছে?
ঘ) কার নেতৃতে, কীভাবে সংঘটিত হয়েছে?
ঙ) শুধু কি বিখ্যাত মানুষেরাই মুক্তিযুদ্ধে অবদান রেখেছিলেন? আমাদের মতো সাধারণ মানুষেরা কী কোন অবদান রেখেছিলেন? তোমাদের পরিচিত কেউ কি মুক্তিযুদ্ধে সরাসরি অংশগ্রহণ অথবা সহযোগিতা করেছিলেন?
চ) করলে, কী ধরনের ভূমিকা রেখেছিলেন?
শহিদ আজাদের গল্প শুনি
এই প্রশ্নগুলো নিয়ে আলোচনার এক পর্যায়ে খুশি আপা মুক্তিযুদ্ধে সাধারণ মানুষের অবদান নিয়ে বলতে গিয়ে শহিদ আজাদের গল্প বললেন-
তোমরা হয়তো অনেকে শহিদ আজাদ এর কথা শুনেছো। মুক্তিযুদ্ধের সময় আজান ছিল তরতাজা এক তরুণ। কম বয়স হলেও সে ছিল ক্র্যাক প্লাটুন নামে একটি গেরিলা দলের ভীষণ সাহসী এক সদস্য। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর উপর গেরিলা আক্রমণ চালাতে বিন্দুমাত্র ভয় পেও না। যুদ্ধের এক পর্যায়ে আজান পাকিস্তানি বাহিনীর কাছে ধরা পড়ে যায়। আজাদের মা অনেক খোঁজাখুঁজি করে জানতে পারেন যে, আজাদকে রমনা থানায় আটকে রাখা হয়েছে। তিনি দিয়ে দেখেন আজানকে এমনই অত্যাচার করা হয়েছে যে আজান উঠে দাঁড়াতে পারছে না। মাকে দেখে আজান বলল যে, বলেছে যদি আজাদ তার গেরিলা দলের বাকি সদস্যদের খবর জানায় তাহলে তাকে ছেড়ে দেবে। আজাদের তখন আজাদকে বলেন জীবন গেলেও যাতে আজান অন্য মুক্তিযোধাদের নাম ঠিকানা না। বলে। আজান সম্মত হয়। দীর্ঘ অনাহারে শী আজাদ মায়ের কাছে ভাত খেতে চেয়েছিল। আজাদের মা ভাত নিয়ে ফেরৎ এসে আজাদকে আর খুঁজে পান নি কখনও। আজাদের মা এরপর যে ১৪ বছর বেঁচে ছিলেন কখনও আর ভাত খান নি।
এ তো গেল এক শহিদ আজাদের কথা। এরকম হাজারো শহিদ আজাদ আমাদের প্রতিটি এলাকায় ছড়িয়ে আছে। আমরা কি কখনও জানবো না আমাদের এলাকায় ছড়িয়ে থাকা এমন বীর শহিদদের কথা? এমন বীর মায়েদের কথা?
নিশ্চয়ই জানবো। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, জানবো কীভাবে? আমাদের এলাকার এই ইতিহাস তো কোথাও লেখা নেই। আমরা কি শুধু অন্যদের খুঁজে পাওয়া ইতিহাস পড়াতেই সীমাবদ্ধ থাকবো ? না নিজেরাই বিস্মৃতির অতল থেকে হারাতে বসা ইতিহাস খুঁজে বের করে আনবো? কেমন হয়, যদি আমরা আমাদের এলাকায় মুক্তিযুদ্ধে সাধারণ মানুষের ভূমিকা অনুসন্ধান করে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে নতুন অধ্যায় যুক্ত করি?
- ক্লাসের সবাই একসাথে বলে উঠলো, আমরা মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে নতুন অধ্যায় যুক্ত করতে চাই।
- খুশি আপা তখন বললেন, আমাদের এলাকার মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে তোমরা কী কী জানতে চাও?
- অনুসন্ধান বললো- কী ঘটেছিল, পাকিস্তানিরা এই এলাকায় কী অত্যাচার করেছিল?
- প্রকৃতির প্রশ্ন, এলাকায় মুক্তিযোদ্ধারা কী করেছিল? স্বাধীনের জানতে চাওয়া-সাধারণ মানুষ কী করেছিল?
সবার প্রশ্ন বোর্ডে লিখে নিয়েছিলেন খুশি আপা। আলোচনা শেষে সবার প্রশ্নগুলোকে কয়েকটি মূল প্রশ্নে ভাগ করা হল।
সবাই মিলে এই প্রকল্পের মধ্য দিয়ে এগুলোর উত্তর খুঁজে বের করবে। যেমন-
১. মুক্তিযুদ্ধের সময় এই অঞ্চলের সাধারণ মানুষের উপর কিরকম অত্যাচার হয়েছিল
২. মুক্তিযোদ্ধারা কীভাবে পাকিস্তানি সেনাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল?
৩. সাধারণ মানুষ কীভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য করেছিল?
চলো প্রকৃতি, অনুসন্ধান ও তার বন্ধুদের মতো আমরাও এই প্রশ্নগুলোর উত্তর খোঁজার জন্য আমাদের প্রকল্পভিত্তিক কাজের পরিকল্পনা করি। |
প্রস্তুতি (দলগঠন ও কর্মপরিকল্পনা)
মিলি জানতে চাইলো যে, কাজটি আমরা কীভাবে করবো? একা একা না সবাই মিলো? খুশি আপা বললেন, তোমরা কীভাবে করলে ভালো হবে বলে মনে করো?
স্বাধীন বললো একা একা কাজটি করা আমাদের জন্য বেশ চ্যালেঞ্জিং হতে পারে। আবার সবাই মিলে করতে গেলেও গোল বেধে যেতে পারে। তাহলে মনে হয়ে ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে করলে ভালো হয়। জয় বললো: ক্লাসে তো আমরা এক এক জন ভিন্ন ভিন্ন এলাকা থেকে এসেছি। আমার মনে হয় একই এলাকায় বাস করে এমন সবাইকে একই দলে রাখলে কাজ করতে সুবিধা হবে। আরেক বন্ধু মোবারক যুক্ত করলো- তবে সংখ্যাটি ৬ থেকে ৮ জনের মাঝে সীমাবদ্ধ থাকলেই ভালো হয়। বেশি হলে সবার অংশগ্রহণ কষ্টকর হতে পারে। এবারে মিলি বললো, তবে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সবাই যাতে একই দলে কাজ করতে পারে তা নিশ্চিত করতে হবে। খুশি আপা বললেন, এই তো তাহলে আমরা এসব বিবেচনায় নিয়ে চল এবার দল গঠন করে ফেলি। সবাই তখন যার যার এলাকা অনুযায়ী ৬ থেকে ৮ জনের দল গঠন করে ফেললো। দল গঠনের আলোচনা শেষে খুশি আপা জানতে চাইলেন, ক্লাসে কারো পরিবারের কেউ মুক্তিযুদ্ধে শহিদ হয়েছেন কিনা?
রবিন বললো, আমার বড় চাচা মুক্তিযুদ্ধে শহিদ হয়েছেন।
খুশি আপা রবিনকে তার চাচার শহিদ হওয়ার ঘটনা সবাইকে শোনানোর অনুরোধ করলে রবিন সবাইকে ঘটনাটা বললো।
এ পর্যায়ে খুশি আপা জানতে চান যে, মুক্তিযুদ্ধের সময়ে এই অঞ্চলে যে এরকম আরও অনেক ঘটনা ঘটেছিল। সেসব কথা কোথা থেকে জানা যেতে পারে?
মুক্তি বললো, এলাকার বিভিন্ন বয়স্ক মানুষের কাছ থেকে।
স্বাধীন পাঠ্যবইয়ে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে যেসব তথ্য আছে সেখান থেকে।
অনুসন্ধান বলল, স্থানীয় লাইব্রেরি থেকে। প্রকৃতির উত্তর, ওই সময়ের পত্রপত্রিকা থেকে। মিলি বলল, শুনেছি
ইন্টারনেটে বিভিন্ন ওয়েবসাইট থেকেও অনেক তথ্য জানা যায় ইত্যাদি। খুশি আপা এবার চিন্তিত ভঙ্গিতে বললেন, এসব উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্য সঠিক কিনা তা কীভাবে জানব? সবাই বেশ চিন্তিত হয়ে পড়লো। জয় বললো, আমরা কয়েক জায়গা থেকে তথ্য নিয়ে মিলিয়ে দেখতে পারি, যদি মিলে যায় তাহলে বুঝবো প্রাপ্ত তথ্য সঠিক।
খুশি আপা বললেন, এবার পরিকল্পনার পালা। তোমরা নিশ্চয় ভুলে যাও নি এর আগে আমরা বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধন পদ্ধতির ধাপসমূহ শিখেছিলাম। এখানে পরিকল্পনা করার জন্য আমরা বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধন পদ্ধতির ধাপসমূহ ব্যবহার করতে পারি। এবার আমাদের এলাকায় মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক প্রকল্পের কাজটি কীভাবে করা যেতে পারে খুশি আপার সহযোগিতায় অনুসন্ধান ও তার বন্ধুরা তার একটি পরিকল্পনা তৈরি করলো।
এবারে চলো আমরাও ওদের মতো প্রকল্পভিত্তিক কাজের মাধ্যমে আমাদের এলাকায় মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস খুঁজে বের করার জন্য পরিকল্পনা তৈরি করি। |
|---|
দলের নিয়ম-নীতি
খুশি আপা মূল কাজ শুরু করার পূর্বে দীর্ঘমেয়াদি এই কাজে দলের সদস্যরা কোনো নিয়ম-নীতি মেনে চলবে কিনা জানতে চাইলে সবাই নানা রকম মতামত দিলো। সেসব মতামত যাচাই-বাছাই করে শিক্ষার্থীদের পালনীয় নিয়ম-নীতির একটি তালিকা তৈরি করলো এবং সকলে অনুসরণ করার জন্য একমত হলো। প্রকৃতি ও তার বন্ধুরা যে তালিকা তৈরি করলো তার কয়েকটি নিয়ম নিচে উল্লেখ করা হলো। এগুলো নিয়ম-নীতির কিছু উদাহরণ মাত্র, অন্যরা চাইলে অন্যভাবেও পরিস্থিতি অনুযায়ী তাদের নিয়ম-নীতি তৈরি করে নিতে। পারে। এবারে চলো আমরাও আমাদের কাজের জন্য সুবিধাজনক একটি নিয়ম-নীতির তালিকা তৈরি করি।
শিক্ষার্থীদের পালনীয় নিয়ম-নীতি
| ১ | কাজ করার সময় সকল সদস্যের প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করা |
|---|---|
| ২ | দলের সবার মতামতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে নিজের মতামত যৌক্তিকভাবে দৃঢ়তার সাথে তুলে ধরা |
| ৩ | নিজের মতামত প্রকাশে কখনও কোনো কারণেই দ্বিধা না করা |
| ৪ | অন্যের মতামত শ্রদ্ধার সাথে যৌক্তিক বিচার-বিশ্লেষণ করে গ্রহণ করা |
| ৫ | দলীয় কাজে ছেলে-মেয়ে ও সক্ষমতার ধরন নির্বিশেষে দলের সকল সদস্যের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা |
| ৬ | সাক্ষাৎকার নেওয়ার আগেই সাক্ষাৎকারদাতার অনুমতি নেওয়া |
| ৭ | |
| ৮ | |
| ৯ | |
| ১০ |
বিদ্যমান তথ্য পর্যালোচনা (লিটারেচার রিভিউ)
আজ খুশি আপা জানতে চাইলেন যে, এই অঞ্চলের মুক্তিযুদ্ধের সময়কার যেসব ঘটনা ইতোমধ্যে সংরক্ষণ করা হয়েছে সেসব কোথায় পাওয়া যাবে? এর উত্তরে সবাই মিলে যা বললো তা একটা তালিকা করলে দাড়ায়-বই, পত্রিকা, ডকুমেন্টারি, দলিলপত্র ইত্যাদি। সবাই মিলে আলোচনা করে তখন ঠিক করলো যে, সব দল প্রয়োজনীয় তথ্যের সম্ভাব্য উৎসের তালিকা তৈরি করবে এবং তালিকা অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ের মাঝে উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করবে এবং তথ্য উৎসের তালিকা, অনুসন্ধান প্রক্রিয়াসহ প্রাপ্ত তথ্যাবলি নিয়ে খুশি আপার সাথে আলোচনা করবে।
পরদিন কাজের অবসরে অদেযার বাসায় নিসর্গ গিয়ে হাজির। ওরা সময় নষ্ট না করে মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক প্রকল্পের কাজ শুরু করে দিতে চায়।
অন্বেষা বলল, এর আগে যে পদ্ধতি অনুসরণ করে আমরা অনুসন্ধান করেছি, এই কাজেও সেই একই পদ্ধতি অনুসরণ করলেই আমাদের হবে। আমার মনে হয় শুধু একটা বিষয় নিয়ে আলাদা করে ভাবা দরকার।
নিসর্গ : কী সেটা?
অন্বেষা: মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে অনুসন্ধান করতে হলে আমাদের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলো আগে জেনে নেয়া দরকার। যদিও এর আগে অনুসন্ধানমূলক কাজের ক্ষেত্রে যে মৌলিক ধাপগুলোর কথা জেনেছিলাম সেখানে বিদ্যমান তথ্য পর্যালোচনা (লিটারেচার রিভিউ) বা ছাপানো বই, পত্র-পত্রিকা, দলিলপত্র পড়ে তথ্য সংগ্রহের ধাপটি ছিল না অনুসন্ধানমূলক কাজের ক্ষেত্রে অনেক সময় বিদ্যমান তথ্য জানা থাকলে নতুন কী তথ্য সংগ্রহ করতে হবে তা নির্ধারণ করা সহজ হয়।
নিসর্গ : তুমি ঠিকই বলেছো। আমার মনে হয় আমরা এ বিষয়ে কিছু বই পড়তে পারি। আর এমন কারো সাথে কথা বলতে পারি যে এ বিষয়ে খুব ভালো জানে। তাহলে তার কাছ থেকে কোনো বই, পত্রিকা এসব পাওয়া যেতে পারে।
দুজনে মুক্তিনের বাসায় গিয়ে মুক্তিকে বলতেই সেও উৎসাহী হয়ে উঠলো। তারপর তিনজনে মিলে মুক্তির দাদাকে গিয়ে ধরলো। মুক্তির দাদা বই পড়তে খুবই পছন্দ করেন। মুক্তি, প্রকৃতি আর অনুসন্ধানের কৌতূহল শুনে তিনি তাঁর ব্যক্তিগত লাইব্রেরি থেকে একগাদা মুক্তিযুদ্ধের বই বের করে আনলেন। তারপর সেগুলো থেকে মজা করে প্রশ্ন করে করে তার উত্তর বলার ঢংয়ে পড়ে শোনাতে লাগলেন।
মুক্তিযুদ্ধ যেন করে হয়েছিল?
তোমরা বোধহয় শুনে মুচকি হাসছ। কে না জানে মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল ১৯৭১ সনে। তবুও জানতে ইচ্ছে করে এটি কেন মুক্তিযুদ্ধ? কেন?
খুব সহজ কথা-মুক্তির জন্য যুদ্ধ। হ্যাঁ, এবার প্রশ্ন উঠবে, কার মুক্তি? কার কাছ থেকে? কেনইবা মুক্তির প্রশ্ন উঠল?
তোমরা আসলে জানো সবই। আমাদের মুক্তি, এই বাংলার অর্থাৎ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের, জনগণের মুক্তি। মুক্তি চেয়েছি আমরা পাকিস্তানের কাছ থেকে। কেন চেয়েছি মুক্তি, তার অনেক কারণ আছে। সেই কারণগুলোও যে তোমরা জানো না তা নয়। একটু ভাব, কিংবা চলো নিজেদের মধ্যে আলোচনা করি। ঠিক বেরিয়ে আসবে কারণগুলো।
সেটা বুঝতে হলে যে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা জরুরি তা হলো-
- মাতৃভাষার অধিকার রক্ষার আন্দোলন
- বৈষম্য ও বঞ্চ
- প্রতিকারে ছয়দফার আন্দোলন
- ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান
- ১৯৭০ এর নির্বাচনে বিজয় ও পাকিস্তানের ষড়যন্ত্র
বিষয়গুলো নিয়ে এই সব বই থেকে সংক্ষেপে তোমাদের জানিয়ে দিচ্ছি। তোমাদের শিক্ষক এবং অন্যান্য আরও অনেক বই-পুস্তক বা এলাকার বয়স্কদের কাছ থেকেও কিছু জানতে পারবে।
ভাষা আন্দোলন
ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে তোমরা অনেকটাই জান। তবুও ছোট করে বলি। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরপরই নতুন দেশের রাষ্ট্রভাষা কী হবে সেই প্রশ্নটা ওঠে। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের চাপ ছিল উর্দু ভাষাকেই রাষ্ট্রভাষা করার। অথচ বাংলা ছিল পূর্ববাংলা তথা পাকিস্তানের বেশির ভাগ মানুষের মাতৃভাষা। পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে পূর্ব বাংলার জনসংখ্যা ছিল অনেক বেশি, তারপরও রাষ্ট্রভাষার বিষয়ে তাদের দাবি উপেক্ষিত হয়, এটা অন্যায়। দেশের বুদ্ধিজীবী, শিক্ষক, সাহিত্যিকরা তাই প্রতিবাদ জানান সঙ্গে সঙ্গে। ছাত্র-ছাত্রীরাও প্রতিবাদে ফেটে পড়েছিল। কিন্তু পাকিস্তান সরকারের জেদ এতটাই ছিল যে, রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে আয়োজিত ছাত্রদের সমাবেশে পুলিশ গুলি চালিয়েছিল, তাতে কয়েকজন নিহত হন। এঁরা হলেন ভাষা শহীদ আবুল বরকত, আব্দুস সালাম, রফিকউদ্দিন আহমেদ, আব্দুল জব্বার ও শফিউর রহমান প্রমুখ।
শেষ পর্যন্ত বাংলাভাষার অধিকার রক্ষার দাবি পাকিস্তান সরকার মানতে বাধ্য হয়েছিল। অন্যায়ের কাছে মাথা নত না করে আমরা বিজয়ী হয়েছিলাম। সাহিত্যিক আবুল ফজল ভাই লিখেছিলেন – একুশ মানে মাথা নত না করা।
বঞ্চনা ও বৈষম্য
গোড়া থেকেই পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার বাঙালিদের প্রতি বৈষম্য চালিয়ে আসছিল। কয়েকটা হিসেব তোমাদের দিচ্ছি, তা থেকে বিষয়টা স্পষ্ট বুঝতে পারবে। তবে তার আগে বুঝে নেওয়া দরকার বৈষম্য বলতে কী বোঝায়? সহজ কথায় বৈষম্য মানে কোনো বিষয়ে সমতা বা ন্যায়সঙ্গত ভাগ না হয়ে অন্যায়ভাবে প্রভেদ করা বা অসমভাবে বণ্টন করা। কয়েকটা দৃষ্টান্ত দিলেই কথাটা পরিষ্কার হবে।
রাজনৈতিক ক্ষেত্রে:
প্রথমত: পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকেরা প্রথম থেকেই পূর্ব পাকিস্তানকে স্বায়ত্বশাসন দিতে অনীহা দেখায়। দ্বিতীয়ত: পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ বাঙালী হওয়া সত্ত্বেও পাকিস্তানের মন্ত্রীসভায় বাঙালীর সংখ্যা ছিল খুবই কম।
১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্টের সরকারকে অন্যায়ভাবে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দেয়া হয়।
প্রশাসনিক ক্ষেত্রে বৈষম্য
১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় প্রশাসনের ৪২০০০ জন কর্মকর্তার মধ্যে বাঙালী ছিল মাত্র ২৯০০ জন। ১৯৬২ সালে পাকিস্তানের মন্ত্রণালয়গুলোতে ৯৫৪ জন শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তার মধ্যে বাঙালী ছিলেন মাত্র ১১৯ জন।
সামরিক ক্ষেত্রে বৈষম্য
সামরিক বাহিনীতে নিয়োগের কোটা ছিল পাঞ্জাবী ৬০%, পাঠান ৩৫% এবং পশ্চিম পাকিস্তানের অন্যান্য অংশ ও পূর্ব পাকিস্তান মিলে অবশিষ্ট ৫%। অবশ্য বাঙালীর দাবীর মুখে এ সংখ্যা পরবর্তীতে কিছুটা পরিবর্তন করা হয়।
১৯৬৬ সালে পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর মোট ১৭ জন শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তার মধ্যে বাঙালী ছিলেন মাত্র জন।
অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বৈষম্য
১৯৪৯-৫০ অর্থবছরে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের মাথাপিছু আয় ছিল ৩০৫ টাকা আর পশ্চিম পাকিস্তানের ছিল ৩৩০ টাকা। ১৯৬৭-৬৮ সালে এই বৈষম্য বেড়ে পূর্ব পাকিস্তানের ক্ষেত্রে হয় ৩৫২ টাকা অথচ পশ্চিম পাকিস্তানের ক্ষেত্রে এটা বেড়ে দাঁড়ায় ৫৩০ টাকায়। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় ব্যাংকসহ প্রায় সকল ব্যাংক, বীমা ও বাণিজ্য কোম্পানীর সদর দফতর ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে। পাকিস্তানের প্রথম পাঁচ বছর মেয়াদি পরিকল্পনায় পূর্বপাকিস্তানের বা বর্তমান বাংলাদেশের জ বরাদ্দ ছিল ১১৩ কোটি রুপি। অথচ পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য বরাদ্দ ছিল ৫০০ কোটি রুপি। ১৯৫৬ সালে শুধু করাচির
উন্নয়নের জন্য ব্যয় করা হয় বাজেটের মোট ব্যয়ের ৫৬.৪% (৫৭০ কোটি টাকা। অথচ পুরো পূর্ব পাকিস্তানের জন্য ব্যয় করা হয় বাজেটের মাত্র ৫.১০%। নতুন রাজধানী ইসলামাবাদ নির্মাণের জন্য ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত বায় করা হয় ৩০০ কোটি টাকা। অথচ ঢাকা শহরের জন্য ব্যয় কর হয় মাত্র ২৫ কোটি টাকা।
পাকিস্তান সরকার এরকম অসংখ্য বৈষম্য সৃষ্টি করে রাষ্ট্র পরিচালনায়। ফলে এর প্রতিবাদে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে স্বাধিকার ও স্বাধীনতা আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে।
প্রতিকারে ছয়দফা
পূর্বপাকিস্তানের জনগণ ও রাজনীতিকদের মধ্যে তখন সাহস ও উদ্যমে আস্থাভাজন নেতা শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি এই বৈষম্য ও বঞ্চনার অবসান চেয়েছিলেন। তিনি চেয়েছেন পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে সম্পদ, সুযোগ ও অন্য সব বিষয়ে সমতা থাকুক। কেন আমরা অন্যায় মেনে নেব? এটা তিনি মানতে পারেন নি। তাই তিনি ঘোষণা করলেন বিখ্যাত ছয়দফা দাবি। এটা ১৯৬৬ সালের কথা। এতে প্রত্যেক প্রদেশ যাতে যার যার সম্পদ ভোগ করতে পারে, রপ্তানি করে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা নিজেদের কাছে রাখতে পারে, খাজনার টাকায় প্রদেশের খরচ নির্বাহ করতে পারে এমন সব দাবি ছিল।
গণঅভ্যুত্থান
তখন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট একজন সামরিক কর্মকর্তা জেনারেল আইয়ুব খান। তিনি অস্ত্রের ভাষায়: জবাব দেওয়ার হুমকি দিলেন। পরে শেখ মুজিবকে প্রধান করে ৩৫ জন আসামীর বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার মামলা ঠুকে দিলেন। এটি ঐতিহাসিক আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা নামে পরিচিত। তাতে অবশ্য উল্টো ফল হলো। জনগণ তাদের প্রিয় নেতার মুক্তির জন্যে এমন আন্দোলন শুরু করল যে আইয়ুব খানকেই ক্ষমতা ছাড়তে হলো। তখন মানুষের মুখে মুখে শ্লোগান ছিল – জেলের তালা ভাঙবো শেখ মুজিবকে আনবো। এটিই - ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান, এই আন্দোলনে ছাত্র-ছাত্রী ও জনতা একেবারে রাজপথ কাঁপিয়ে দিয়েছিল। তরুণ আসাদ ও কিশোর মতিউরসহ অনেকেই শহিদ হয়েছিল। পুলিশ, মিলিটারি নামিয়েও আন্দেলন থামানো যায়, নি। এমনকি ছাত্র ও শ্রমিকের মৃত্যুতেও মানুষ পিছপা হয় নি। এই সময়ে মুক্ত শেখ মুজিবকে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ বঙ্গবন্ধু উপাধিতে ভূষিত করেছিল।
সত্তরের নির্বাচন
আইয়ুব খানের পরে আরেক সামরিক কর্মকর্তা জেনারেল ইয়াহিয়া খান এলেন ক্ষমতায়। তিনি বুঝলেন আগের মতো চললে হবে না। তাই নতুন সংবিধান রচনা ও দ্রুত একটি জাতীয় নির্বাচনের প্রতিশ্রুতি দিলেন। নির্বাচন হলো ১৯৭০ সালের ডিসেম্বরের ৭ তারিখ। সরকার ভেবেছিল শেখ মুজিবের দল আওয়ামী লীগ কিছু আসন পেলেও দুই প্রদেশ মিলিয়ে সরকার গঠনের মতো সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে না। কিন্তু হলো কি, নিরঙ্কুশ বিজয় (অর্থ হচ্ছে বিরাট ব্যবধানে একচেটিয়া বিজয়। ইংরেজিতে landslide victory, শাব্দিক মানে ভূমিধস বিজয়) পেল আওয়ামী লীগ। পাকিস্তানের জাতীয় সংসদের মোট ৩০০ জন প্রতিনিধির মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য বরাদ্দ ছিল মোট ১৬৯ জন। এই ১৬৯ জনের মধ্যে ২টি ছাড়া বাকি ১৬৭ জন সদস্যই নির্বাচিত হয়েছিলেন আওয়ামী লীগের প্রার্থীদের মধ্য থেকে। দ্যাখো পাকিস্তান জাতীয় সংসদের মোট সদস্য। সংখ্যা হলো ৩০০, তাহলে ১৫১ প্রার্থী বিজয়ী হলেই তো একটি দল সরকার গঠন করতে পারে। আওয়ামী লীগের ১৬৭ জন প্রার্থী জয় লাভ করেছে। ফলে তারাই কেন্দ্রে সরকার গঠন করার ন্যায্য দাবিদার। বঙ্গবন্ধু হবেন পাকিস্তানের প্রথম নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী। কিন্তু এটা পাকিস্তানি অধিকাংশ রাজনীতিক, মিলিটারি বা সামরিক কর্মকর্তা, সরকারি কর্মকর্তা, আমলাতন্ত্র কিছুতেই মানতে পারে নি। ফলে তারা নানা রকম ষড়যন্ত্র পাকাতে শুরু করে।
ওদের ষড়যন্ত্র আমাদের অসহযোগ
এইভাবে এসে গেল ১৯৭১ সাল। ঠিক হলো পয়লা মার্চ ঢাকায় জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন বসবে। কিন্তু পাকিস্তানের তো সেই এক রোগ - বাঙালির নেতৃত্ব মানবে না। পাকিস্তানের রাজনীতিবিদ জুলফিকার আলী ভুট্টো ছিলেন অত্যন্ত উচ্চাভিলাষী। তিনি কয়েকজন সামরিক কর্মকর্তার সাথে গোপন ষড়যন্ত্র আঁটলেন, তাতে রাষ্ট্রপতি ইয়াহিয়া খানকেও যুক্ত করে নেয় তারা। মূল লক্ষ্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের হাতে পাকিস্তানের ক্ষমতা না দেওয়া। ভুট্টোর চাপে পয়লা মার্চের অধিবেশন বন্ধ করেন ইয়াহিয়া খান। আর তাতে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ ক্ষোভে ক্রোধে রাজপথে নেমে আসে। বঙ্গবন্ধুও জোরালো ভাষায় প্রতিবাদ জানালেন আর শুরু করলেন অসহযোগ আন্দোলন। অসহযোগ আন্দোলন নিয়ে দুটো কথা বলে নিই। অসহযোগ মানে সহযোগিতা না করা। আর তা আন্দোলনে রূপ নেয় যখন কোনো জনগোষ্ঠী কোনো কর্তৃপক্ষের সাথে অসহযোগিতা শুরু করে। বঙ্গবন্ধু পাকিস্তান সরকারের সাথে অসহযোগিতার ডাক দিয়েছিলেন। অর্থাৎ সরকারি কর্মীরা কাজে যোগ দেবেন না, সব অফিস:আদালত, স্কুল-কলেজ বন্ধ থাকবে। এভাবেও সরকারকে দাবি মানতে বাধ্য করা যায়। ব্রিটিশ আমলে মহাত্মা গাভি এ ধরনের আন্দোলন প্রথম শুরু করেছিলেন।
৭ই মার্চের পর বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে বাংলাদেশের সকল স্কুল-কলেজ, অফিস-আদালত, কল-কারখানা বন্ধ হয়ে যায়। খাজনা ট্যাক্স আদায় বন্ধ হয়ে যায়। ক্যান্টনমেন্ট ব্যতীত সমস্ত দেশে বঙ্গবন্ধুর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৭১ এর মার্চে বঙ্গবন্ধুর ডাকে সাড়া দিয়ে বাংলাদেশের মানুষ পাকিস্তান সরকারের নির্দেশনা অমান্য করে পূর্ণ অসহযোগিতা করে। ইতিহাসে এটা মার্চের অসহযোগ আন্দোলন নামে পরিচিত।
৭ই মার্চের ভাষণ
এই সময়ের অারেকটি বড় ঘটনা হল ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চে রেসকোর্স ময়দানে লাখো জনতার সামনে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষা। নেতার ওপর জনতার চাপ ছিল স্বাধীনতা ঘোষণার। আর পাকিস্তান এমন সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। বঙ্গবন্ধু সরাসরি স্বাধীনতার ঘোষণা দিলে তারা জনতা ও নেতা সবার ওপরই অস্ত্র নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছিল। তবে আমাদের নেতা ছিলেন দূরদর্শী অভিজ্ঞ মানুষ। তিনি সুকৌশলে এমনভাবে স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে সভা শেষ করলেন যে তাতে সাপও মরল, লাঠিও ভাঙল না কথাটা বলা হলো, আবার ঠিক সরাসরি ঘোষণাও হলো। না। বললেন- 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' এটিই ছিল সবার কাছে স্বাধীনতার বার্তা। আজ তাঁর এই ১৭ মিনিটের তাৎক্ষনিক বলা ভাষাটিকে ইউনেস্কো বিশ্ব ঐতিহ্যের স্বীকৃতি দিয়েছে।
আলোচনা, অপারেশন সার্চলাইট ও গণহত্যা
পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে দেখে এবার তারা আন্দোলন থামাতে আলোচনার প্রস্তাব দিলো। গণতন্ত্রে বিশ্বাসী বঙ্গবন্ধু তাতে সায় দিলেন। কিন্তু আলোচনার আড়ালে তারা পূর্ব পাকিস্তানের সেনানিবাসগুলোতে সৈন্য সমাবেশ আর অস্ত্র জমা করেছে।
এক সময় তাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী আলোচনা ভেঙে দিয়ে ২৫ মার্চ সন্ধ্যার মধ্যে ইয়াহিয়া খানসহ ওরা ফিরে গেল পশ্চিম পাকিস্তানে। আর সেদিন মধ্যরাতে শুরু হলো ইতিহাসের ভয়ঙ্কর নির্মম হত্যাযজ্ঞ- অপারেশন সার্চলাইট। হানাদার পাক সেনাদের আক্রমণের শিকার হলেন ছাত্র-তরুণ, অধ্যাপক, বুদ্ধিজীবী, বিভিন্ন পেশার মানুষ, লেখক, কবি, শিল্পীরা। তারা বিশেষভাবে টার্গেট করেছিল সংখ্যালঘু হিন্দুদের আর আওয়ামী লীগের কর্মী-সমর্থকদের। নয়মাস ধরে এ-ই চলেছে। এভাবে নয়মাসে ৩০ লক্ষ মানুষ শহিদ হয়েছেন। বাঙালি নারীদের নির্যাতনেও তারা পিছিয়ে ছিল না।
বঙ্গবন্ধুর সিদ্ধান্ত ও স্বাধীনতার ঘোষণা
এদিকে বঙ্গবন্ধু সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি নিজ বাড়িতে অবস্থান করে ভাগ্যে যা থাকে তা বরণ করবেন। এ ব্যাপারে তাঁর দুটি বিবেচনা কাজ করেছে- প্রথমত, তিনি মনে করলেন হানাদার বাহিনী তাঁকে না পেলে ঢাকা শহরে ধ্বংসযজ্ঞ চালাবে। দ্বিতীয়ত, তাঁর মনে হয়েছে তিনি এতই পরিচিত একটি মুখ যে তাঁর পক্ষে আত্মগোপন করা সম্ভব নয়। পলাতক অবস্থায় ধরা পড়লে তা হবে লজ্জাজনক। এর চেয়ে সাহসিকতার সঙ্গে ওদের মুখোমুখী হলে সেটা সবার জন্যে মঙ্গলজনক হবে। তবে গ্রেফতার হবার আগে ২৫ মার্চ রাত ১২টার পর অর্থাৎ ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে তিনি স্বাধীনতার একটি ঘোষণা প্রচারের জন্যে ইপি আর বাহিনীর কাছে প্রেরণ করেন। এই ঘোষণা ইপি আর-এর ওয়্যারলেসের মাধ্যমে প্রথমে চট্টগ্রামে প্রেরণ করা হয়। পরে দেশের অন্যান্য জায়গাতেও এটি পাঠানো হয়েছিল। এটিই আমাদের স্বাধীনতার ঘোষণা। ঘোষণায় তিনি উল্লেখ করেন দখলদার পাকিস্তান বাহিনীর শেষ সৈন্যটিকেও বাংলার মাটি থেকে বিতাড়িত না করা পর্যন্ত যেন বাংলাদেশের জনগণ লড়াই চালিয়ে যায়। শুরু হয় আমাদের মুক্তিযুদ্ধ।
স্বাধীন বাংলা বেতার
চট্টগ্রাম বেতারের কয়েকজন কর্মী প্রবীণ শিল্পী বেলাল মোহাম্মদের নেতৃত্বে কালুরঘাট থেকে স্বাধীনতার পক্ষে একটি বেতারকেন্দ্র চালানোর সিদ্ধান্ত নেন। সে অনুযায়ী তাঁরা কাজ শুরু করেন এবং অনেকেই তাঁদের সঙ্গে যুক্ত হন। এই কেন্দ্র থেকে ২৭ মার্চ সন্ধ্যায় চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম. এ. হান্নান সর্বপ্রথম বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণাটি পাঠ করেন। পরে এটি আরও অনেকেই পাঠ করেছেন। প্রথমদিকে এই কেন্দ্রের নাম রাখা হয়েছিল স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতারকেন্দ্র। পরে যখন কলকাতায় একটি পূর্ণাঙ্গ বেতার কেন্দ্র স্থাপিত হয় তখন এর নাম থেকে বিপ্লবী শব্দটি বাদ দেওয়া হয়। সারাদেশ থেকে শিল্পী- সাহিত্যিক-সাংবাদিক ও বুদ্ধিজীবীরা কলকাতায় এসে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে যুক্ত হন। যুদ্ধের নয় মাস ধরে এই কেন্দ্র থেকে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সঙ্গীত, কথিকা, নাটক এবং অন্যান্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জনগণ ও মুক্তিযোদ্ধাদের উদ্দীপ্ত রাখা হয়। চট্টগ্রাম বেতারের কয়েকজন কর্মী প্রবীণ শিল্পী বেলাল মোহাম্মদের নেতৃত্বে কালুরঘাট থেকে স্বাধীনতার পক্ষে একটি বেতারকেন্দ্র চালানোর সিদ্ধান্ত নেন। সে অনুযায়ী তাঁরা কাজ শুরু করেন এবং অনেকেই তাঁদের সঙ্গে যুক্ত হন। এই কেন্দ্র থেকে ২৭ মার্চ সন্ধ্যায় চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম. এ. হান্নান সর্বপ্রথম বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণাটি পাঠ করেন। পরে এটি আরও অনেকেই পাঠ করেছেন। প্রথমদিকে এই কেন্দ্রের নাম রাখা হয়েছিল স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতারকেন্দ্র। পরে যখন কলকাতায় একটি পূর্ণাঙ্গ বেতার কেন্দ্র স্থাপিত হয় তখন এর নাম থেকে বিপ্লবী শব্দটি বাদ দেওয়া হয়। সারাদেশ থেকে শিল্পী-সাহিত্যিক-সাংবাদিক ও বুদ্ধিজীবীরা কলকাতায় এসে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে যুক্ত হন। যুদ্ধের নয় মাস ধরে এই কেন্দ্র থেকে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সঙ্গীত, কথিকা, নাটক এবং অন্যান্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জনগণ ও মুক্তিযোদ্ধাদের উদ্দীপ্ত রাখা হয়।
গল্পজাতন্ত্রী বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রথম সরকার
তাজউদ্দীন আহমদ দলের জ্যেষ্ঠ নেতা ও সংসদ সদস্যদের সাথে যোগাযোগ করে সরকার গঠনের উদ্যোগ নেন। এই উদ্যোগের মাধ্যমে ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রথম সরকার গঠিত হয়। ১৭ এপ্রিল কুষ্টিয়া জেলার মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলায় এই সরকার শপথ গ্রহণ করে। এই সরকারকে মুজিবনগর সরকার বা প্রবাসী সরকারও বলা হয়। বঙ্গবন্ধুকে তাঁর অনুপস্থিতিতে রাষ্ট্রপতি ঘোষণা করা হয়: এবং সৈয়দ নজরুল ইসলামকে তাঁর অবর্তমানে ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব দেওয়া হয়। তাজউদ্দীন আহমদ প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং ক্যাপ্টেন মনসুর আলী, এ এইচ এম কামারুজ্জামান, ইউসুফ আলীসহ কয়েকজনকে নিয়ে মন্ত্রী পরিষদ গঠিত হয়। কর্ণেল ওসমানিকে জেনারেল পদ দিয়ে সেহাবাহিনীর প্রধান সেনাপতি ঘোষণা করা হয়। এভাবে আনুষ্ঠানিকভাবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের যাত্রা শুরু হল ।
নয়মাসের যুদ্ধ ও বিজয়
যুদ্ধের সময় প্রাণ বাঁচাতে প্রায় এক কোটি মানুষ ভারতে আশ্রয় নিয়েছিল। ভারত কেবল তাদের আশ্রয়ই দেয় নি, বাংলাদেশ যে প্রবাসী সরকার গঠন করেছিল তাকে অফিসের জায়গা দিয়েছিল, গেরিলাদের প্রশিক্ষণ ও অস্ত্র দিয়েছিল, নৌ কমাণ্ডো গঠন, বিমান বছর তৈরি, নিয়মিত বাহিনী গঠনে সর্বাত্মক সহযোগিতা নিয়েছিল। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ভারসাম্য রক্ষা ও অন্যান্য দেশের সমর্থন আদায়েও ভারত সরকার সচেষ্ট ছিল। শেষে বাংলাদেশের সাথে যৌথ বাহিনী গঠন করে সরাসরি যুদ্ধের মাধ্যমে পাকিস্তানের পরাজয়ে কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে। তাদেরও প্রায় ৬-৭ হাজার সৈনিক এই যুদ্ধে প্রাণ হারায়।
অবশেষে নয়মাস পরে ১৬ ডিসেম্বর বিকেল বেলা ঢাকায় রেসকোর্স ময়দানে আনুষ্ঠানিকভাবে পাকিস্তানি বাহিনী যৌথ বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে। আমরা হানাদার মুক্ত হলাম। বঙ্গবন্ধুর ভাষায় ওরা আমাদের নাবায়ে রাখতে পারে নি। আমরা বিজয়ী হলাম, স্বাধীন হলাম। বিশ্বের মানচিত্রে লাল-সবুজ পতাকার নতুন রাষ্ট্র মাথা তুলে नাঁড়াল।
সর্বস্তরের মানুষের অংশগ্রহ
একটু খেয়াল করে দ্যাখো পাকিস্তানি সেনাবাহিনী যখন হত্যা চালিয়েছে তখন কিন্তু ধনী-দরিদ্র, শিক্ষিত নিরক্ষর, ধর্ম-বর্ণ- জাতি, নারী-পুরুষ এসব বিচার করে নি। তারা বাঙালিদের হত্যা করেছিল। পঁচিশে মার্চ রাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশ্বখ্যাত পণ্ডিতদের যেমন মেরেছে তেমনি নিরক্ষর পরি রিক্সাচালক বা বস্তিবাসীদেরও গুলি করে হত্যা করেছে।
পাকিস্তান আমলে ২২ পরিবারের কথা বলা হতো। এরা ছিল অভিধনী। এই তালিকায় একজন মাত্র বাঙালি ছিলেন। তাঁকেও কিন্তু একাত্তরে নিজের বাড়ি ছেড়ে পরিবার নিয়ে পালাতে হয়েছিল। আবার ছাত্র, শিক্ষক, মজুররাও পালিয়ে ছিল। মোটকথা সর্বস্তরের বাঙালিকেই সেদিন বাড়িঘর দেশ ছেড়ে শরণার্থী হতে হয়েছিল।
আবার এদের মধ্য থেকেই তরুণ-তরুণীরা দলে দলে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছে। গেরিলা যুদ্ধে, নৌ কমাণ্ডো হিসেবে বা নিয়মিত বাহিনীর সদস্য হিসেবে সর্বস্তরের তরুণ-তরুণীরা মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিল। তোমরা একটা কাজ করতে পার। প্রত্যেক পরিবারেই খোঁজ করলে মুক্তিযোদ্ধার খবর পেয়ে যাবে। তাঁদের অভিজ্ঞতাগুলো শুনে লিখে ফেলবে। তারপর স্কুলে এসে পরস্পরের লেখাগুলো শুনে নিতে পারো। তাহলেই বুঝতে পারবে সমাজের সব স্তরের সব ধর্মের মানুষ এতে যুক্ত হয়েছিলেন। এমনকি নারীরাও পিছিয়ে থাকেন। নিঃ তোমরা নিশ্চয় তারামন বিবি, কাঁকন বিবি এঁদের নাম শুনেছো।
গেরিলা যুদ্ধ:
আরেকটা বিষয়ও খুব গুরুত্বপূর্ণ। মুক্তিযুদ্ধে দুই পক্ষের সেনাদের মধ্যে সনাতন ধারার যুদ্ধ হয়েছে শেষের দিকে। তার আগে মূলত চলেছে গেরিলা যুদ্ধ। গেরিলারা ছদ্মবেশে সাধারণ মানুষের মধ্যে মিশে থেকে পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী হঠাৎ করেই আক্রমণ চালিয়ে আবার ভীড়ের মধ্যে মিশে যায়। একে বলে 'হিট অ্যাড রানা পদ্ধতি, অর্থাৎ আক্রমণ করেই পালিয়ে যাও। ফলে গেরিলাদের দেশের ভিতর গোপন আস্তানা দরকার ছিল, গোলাবারুদ রাখার নিরাপদ স্থানের দরকার ছিল, অনেক সময় চলাচলের জন্য নির্ভরযোগ্য মানুষের গাড়ি, নৌকা বা রিক্সারও প্রয়োজন হতো। তাই মনে রাখতে হবে অনেক পরিবার এভাবে মুক্তিযুদ্ধে অবদান রেখেছেন। গৃহিণীরা গেরিলাদের খাবার ব্যবস্থা করেছেন, আবার ছোট ছেলেমেয়েরা খবর আদান-প্রদানে সহায়তা করেছে। ফলে অস্ত্র হাতে যুদ্ধ না করেও মুক্তিযুদ্ধে ভূমিকা রেখেছেন অনেকে। তোমরা হয়তো শহিদ সুরকার আলতাফ মাহমুদের কথা জানো। ইনিই আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি- এই বিখ্যাত গানে সুর নিয়েছিলেন। শহিদ জননী জাহানারা ইমামের একাত্তরের দিনগুলো থেকে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে গেরিলা আক্রমণের ঘটনাটাও পড়ে নিতে পারো। পাশাপাশি একজন গেরিলা বা এ ধরনের অভিযানে প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালনকারী মানুষের কাছ থেকে সরাসরি তাঁর অভিজ্ঞতা শুনতে পারলে তাও হবে এক বিরাট প্রাপ্তি। চেষ্টা করে দেখতে পারো এমন কাউকে খুঁজে পাও কিনা।
প্রকৃতি ও জলবায়ুর ভূমিকা
আরেকটা বিষয় জানলে ভালো লাগবে। জানোই তো বাংলাদেশ হলো নদীমাতৃক দেশ। এদেশে সাতশয়ের বেশি নদনদী-খাল আছে। এর বাইরে বিল, ঝিল আর জলাভূমি তো অসংখ্য। সব গাঁয়েই যেন নদী নয়ত খাল রয়েছে, তার ওপরে আছে বর্ষার প্রকোপ। একাত্তরে বর্ষা ছিল অনেকদিন, তাতে বছরের বেশির ভাগ সময় নদী-খাল-বিল ছিল ভরাট, কাদায় পথচলা ছিল কষ্টকর। গেরিলা যুদ্ধের জন্যে এমন ভূপ্রকৃতি আর জলবায়ু খুব উপযোগী। পাকিস্তানিরা কিন্তু গেরিলা যোদ্ধা ছিল না, তারা সনাতন পদ্ধতির সৈনিক। তার ওপর ওদের দেশ হচ্ছে রুক্ষ, শুষ্ক, ওখানে এতো নদী-নালা-খাল-বিল নেই। ওরা জানত না সাঁতার, ফলে পানিতে ওদের খুব ভয়। এই প্রাকৃতিক পরিবেশও আমাদের জন্যে যুদ্ধে খুব সহায়ক হয়েছিল। এদেশীয় দালাল আলবদর রাজাকার আর শান্তি কমিটির মত বিশ্বাসঘাতকরা না থাকলে ওরা নয়মাসও টিকতে পারতো না, অন্তত গ্রামগঞ্জ সবসময় স্বাধীন থাকতো।
হানাদারদের দোসর
তবে দুর্ভাগ্যের বিষয় আত্মসমর্পণের আগে পাকবাহিনীর সহযোগী এদেশীয় দোসর আলবদর-রাজাকাররা বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ কিছু সন্তানকে হত্যা করে। আসলে ১৯৭১ এ সারা বছর ধরে তারা মানুষ হত্যা করে গেছে। জামায়াতে ইসলামি ও মুসলিম লীগসহ কয়েকটি রাজনৈতিক দল হানাদার পাকিস্তানিনের পক্ষ নিয়েছিল। এদের নেতৃত্বেই গঠিত হয়েছিল শান্তি কমিটি হানাদারদের দালাল ও দোসরের ভূমিকা পালনের জন্যে। এছাড়াও এরা রাজাকার, আলবদর, আল শামস বাহিনী গঠন করে মুক্তিযোদ্ধা এবং মুক্তিযুদ্ধের সমর্থক বুদ্ধিজীবী, শিক্ষক, চিকিৎসক, সাংবাদিক, লেখক শিল্পীদের হত্যার কাজে লাগিয়েছিল। আমরা জানি ৩০ লক্ষ শহিদের বিনিময়ে আমরা এই স্বাধীন দেশ পেয়েছি। তার সাথে যোগ করতে হবে দুই থেকে তিন লক্ষ নারীকে নির্মমভাবে নির্যাতনের ঘটনা। ফলে এই স্বাধীনতা বহু মানুষের আত্মত্যাগে অর্জিত হয়েছে। একদিকে লক্ষ প্রাণের আত্মত্যাগ এবং অন্যদিকে বহু মানুষের বীরত্বব্যঞ্জক ভূমিকায় আমরা লাভ করেছি লাল-সবুজের এই পতাকা। এই পতাকার সম্মান এবং দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করা আমাদের সবার পবিত্র দায়িত্ব।
যুদ্ধদিনের বাংলাদেশ
একটা কথা মনে রেখো এই যুদ্ধে যেমন সর্বস্তরের মানুষ যোগ দিয়েছিল তেমনি দেশের ৬৪ হাজার গ্রামের কোনোটিই হয়তো বাদ ছিল না এ যুদ্ধ থেকে। পাকিস্তানি হানাদাররা প্রায় প্রত্যেক গ্রামে হিন্দু পাড়ায় আগুন দিয়েছে, আওয়ামী লীগের সমর্থকদের বাড়িঘর জ্বালিয়ে দিয়েছে, কোথাও গণহত্যা চালিয়েছে। সারা দেশে কত বধ্যভূমি ছড়িয়ে আছে! ত্রিশ লক্ষ মানুষ হত্যা তো সহজ কাজ নয়। সারা দেশ জুড়ে পুরো নয়মাসব্যাপী এই নির্মম হত্যাযজ্ঞ চলেছে।
ফলে এরকম পরিবেশে ঈদ, পূজা, পার্বণগুলো যথাযথ উৎসবের মতো পালনের মনোভাব মানুষের মধ্যে ছিল। না। থাকবেই বা কী করে। বাড়ির সন্তান হয়তো যুদ্ধে গেছে, আবার কোথাও সন্তান খবর পাঠিয়েছে তার দল রাতে খাবে, কোথাও আহত যোদ্ধার সেবার ব্যবস্থা করতে হবে, কাউকে বা অস্ত্রগুলো নিরাপদে নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে দিতে হবে। অনেক বাড়ির এক বা একাধিক সদস্য তো শহিদ হয়েছিলেন। তাদের পক্ষেও শোক কাটিয়ে উৎসব পালন ছিল কঠিন। প্রতি মুহুর্তে ছিল মৃত্যুর ভয়। দেশ তখন ছিল যেন এক মৃত্যুপুরী। যুদ্ধ তো ঈদ- পার্বনের দিনেও থেমে থাকে নি। ফলে এ ছিল ভিন্ন রকম ঈদ বা পূজা। হ্যাঁ বাড়ির বয়োজ্যেষ্ঠ সদস্যদের কাছ থেকে একাত্তরের উৎসবের দিনগুলোর কথাও জেনে নিতে পারো। সেই বছর একুশে ফেব্রুয়ারি ছিল যুদ্ধের আগে আগে, তাই খুব জোশের সঙ্গে সেটি পালিত হয়েছিল। কিন্তু নববর্ষ পড়েছিল যুদ্ধের ভিতরে, সেটি সেভাবে পালিত হতে পারে নি। যেসব ক্ষুদ্র জাতি নববর্ষ উপলক্ষে বৈসাবি, সাংগ্রাই বা অন্য উৎসব পালন করে তাদের কী অবস্থা ছিল তাও জেনে নেওয়া যায়। এর ভিত্তিতে একাত্তরের উৎসব নামে একটা প্রকল্প তোমরা করতে পার।
একাত্তর সনে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষাও ঠিক মতো হতে পারে নি। কোথাও আগেই প্রচারপত্র বিলি করে পরীক্ষা না দিতে বলেছে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের মানুষজন, কোথাও পরীক্ষাকেন্দ্রের গেইটে লিখে দিয়েছে সে কথা। আর কোথাও কেন্দ্রের আশেপাশে গ্রেনেড হামলা হয়েছে। এ সময় পাকিস্তানের দখলদারিত্বে দেশের কিছুই যে স্বাভাবিক নেই সেটা প্রমাণ করতে হবে না বিশ্বের কাছে। তাই এই ব্যবস্থা।
শেষ কথা
যুদ্ধের নয়মাস দেশ অবরুদ্ধ ছিল, জীবন ছিল অস্বভাবিক। মানুষ কেবল আতঙ্কের মধ্যেও স্বাধীনতার প্রহর গুনেছে, তার জন্যে কাজ করেছে। শামসুর রাহমানের বিখ্যাত 'তোমাকে পাওয়ার জন্যে হে স্বাধীনতা' কবিতাটি পড়ে নিও তোমরা। এখানে কয়েক লাইন আমরা তুলে দিচ্ছি -
তুমি আসবে ব'লে, হে স্বাধীনতা,
সাকিনা বিবির কপাল ভাঙলো, সিঁথির সিঁদুর গেল হরিদাসীর।তুমি আসবে ব'লে, হে স্বাধীনতা, শহরের বুকে জলপাই রঙের ট্যাঙ্ক এলো তুমি আসবে ব'লে, হে স্বাধীনতা, ছাত্রাবাস বস্তি উজাড় হলো। রিকয়েললেস রাইফেল আর মেশিনগান খই ফোটালো যত্রতত্র। তুমি আসবে ব'লে, ছাই হলো গ্রামের পর গ্রাম। তুমি আসবে ব'লে, বিধ্বস্ত পাড়ায় প্রভুর বাস্তুভিটার ভগ্নস্তূপে দাঁড়িয়ে একটানা আর্তনাদ করলো একটা কুকুর দানবের মত চিৎকার করতে করতে
তুমি আসবে ব'লে, হে স্বাধীনতা,
মুক্তির দাদার একনাগাড়ে বলা কথাগুলো তিনজনের মাঝেই একটা ঘোর তৈরি করে দিলো। মনের মধ্যে হাজার প্রশ্ন টগবগ করে ফুটতে শুরু করেছে সবার। প্রশ্নগুলো নিয়ে মনে মনে নাড়াচাড়া করতে করতে নিসর্গ আর অন্বেষা বাড়ি ফিরে এলো। ওরা ঠিক করলো এবার সুন্দর একটা পরিকল্পনা করে কাজে নেমে পড়তে হবে।
অনুসন্ধান ও তথ্য সংগ্রহ
নিসর্গ অদেয়াকে বললো, খুব ভালো একটা কাজ হলো দাদা আর খুশি আপার সহযোগিতায় আমরা বই আর পত্র-পত্রিকা থেকে প্রয়োজনীয় অনেক তথ্য পেলাম। এবার চলো আমরা আমাদের পরিবার ও এলাকার বয়স্ক ব্যক্তি যারা মুক্তিযুদ্ধ দেখেছেন বা মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জানেন তাদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করি।
মালা বললো, সে না হয় করবো কিন্তু তাদের জিজ্ঞাসা করবোটা কী? অদেয়া বললো, ভালো কথা বলেছে। তাহলে চলো আমরা একটা সাক্ষাৎকার গ্রহণের প্রশ্নমালা তৈরি করি।
সাক্ষাৎকার গ্রহণের জন্য প্রশ্নমালা
অনুসন্ধানের জন্য প্রশ্ন | সাক্ষাৎকার গ্রহণের প্রশ্নমালা |
|---|---|
| ১। মুক্তিযুদ্ধের সময় এই অঞ্চলের সাধারণ মানুষের উপর কীরকম অত্যাচার হয়েছিল? | ১। মুক্তিযুদ্ধের সময় আপনি কোথায় ছিলেন? ২। তখন আপনার বয়স কত ছিল? ৩। আপনার জানা মতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী কি এই এলাকায় এসেছিল? ৪। উত্তর হ্যাঁ হলে, তারা কী ধরনের অত্যাচার নিপীড়ন করেছিল? (উপরের নমুনা অনুসারে শিক্ষার্থীরা প্রয়োজনীয় আরও প্রশ্ন তৈরি করে নিতে পারে।) ৫। ৬। ৭। |
| ২। মুক্তিযোদ্ধারা কীভাবে পাকিস্তানি সেনাদের | বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল? | উপরের নমুনা প্রশ্নের মতো শিক্ষার্থীরা তাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণের প্রশ্নমালা তৈরি করে নিতে পারে। ১। ২। ৩। |
| ৩। সাধারণ মানুষ কীভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য করেছিল? | উপরের নমুনা প্রশ্নের মতো শিক্ষার্থীরা তাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণের প্রশ্নমালা তৈরি করে নিতে পারে। ১। ২। ৩। |
সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর নাম: তারিখ: | |
চলো নিসর্গ ও অদেখা আর তার বন্ধুদের মতো আমরাও আমাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণের প্রশ্নমালা তৈরি করি এবং তথ্য সংগ্রহ করি। |
|---|
এরপর নিসর্গ ও অভ্যো আর তাদের বন্ধুগণ দলে ভাগ হয়ে প্রথমে নিজ পরিবার থেকে তথ্য সংগ্রহ করলো। দলের সব সদস্য তাদের প্রাপ্ত তথ্য একত্র করে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করলো। তারা এগুলো নিয়ে খুশি আপার সাথে আলোচনা করলো। এরপর খুশি আপা প্রতিটি দলকে বললেন, দলের সদস্যদের স্বজনদের ঘটনা থেকে অন্তত একটি বিশেষ ঘটনা ক্লাসের সবার সাথে শেয়ার করতে।
- প্রতি দলের উপস্থাপনার পর খুশি আপা তাদের সংগৃহীত ঘটনাবলিতে যেসব জায়গার উল্লেখ পাওয়া গেছে সেখান থেকে নতুন তথ্য পাওয়া যায় কিনা তা অনুসন্ধান করতে বললেন। এই প্রসঙ্গে এই এলাকায় প্রকৃতি ও পরিবেশগত কারণে (যেমন- নদী নালা বেশি থাকার কারণে, ইত্যাদি) পাকিস্তানিরা কোন বাধা পেয়েছে কিনা সেই তথ্যও অনুসন্ধান করতে বললেন। দলগুলো উক্ত জায়গাগুলো খুঁজে বের করলো এবং দলীয় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সেই জায়গা পরিদর্শন করে, প্রত্যক্ষদর্শীদের সাক্ষাৎকার নিয়ে কিংবা বর্ষীয়ান ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকার নিয়ে তথ্য সংগ্রহ করলো। কাজে যাবার আগে দলগুলো শিক্ষকের সাথে দলীয় পরিকল্পনাও শেয়ার করলো।
- খুশি আপা দলগুলোর পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ এগুচ্ছে কি না তার খোঁজ-খবর রাখলেন এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য সকল ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক সহযোগিতা দিলেন। কিন্তু কোন মতামত চাপিয়ে না দিয়ে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিলেন এবং প্রয়োজনে কারিগরি। যেমন- তথ্য সংগ্রহের জন্য রেকর্ডার, ক্যামেরা ইত্যাদি) ও প্রশাসনিক। যেমন- কোন জায়গায় প্রবেশ করতে বিশেষ অনুমতি দরকার হলে প্রধান শিক্ষকের পরামর্শক্রমে চিঠি দেওয়া) সহায়তা দিলেন।
- দলগুলো নিজ নিজ এলাকায় / লোকালয়ে মুক্তিযুদ্ধকালীন অবস্থা / ঘটনা উল্লেখযোগ্য স্থান/ সমাজের একক ব্যক্তি/পরিবার/দলগতভাবে মানুষের অবদান সম্পর্কে বর্ষীয়ান বা তথ্য ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করলো। মুক্তিযুদ্ধকালীন স্থানীয় জনগণের বাস্তব অবস্থা, প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ এবং মুক্তিযুদ্ধের আন্তঃসম্পর্ক, অসাম্প্রদায়িক পরিবেশ, বিভিন্ন উৎসব উদযাপন ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনার মাঝে আন্তঃসম্পর্ক, মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি ও ঘটনাবলি সম্বলিত স্থান বা প্রত্যক্ষদর্শী প্রভৃতি সম্পর্কে জানার চেষ্টা করলো এবং গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসমূহ দলের সদস্যরা নোট করে নিলো। প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে তারা বিভিন্ন প্রতীক, চিহ্ন ব্যবহার করে এলাকায় মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি সম্বলিত স্থানসমূহ চিহ্নিত করে মানচিত্র তৈরি করলো।
চলো আমরাও আমাদের কাজের একটি মানচিত্র তৈরি করি |
|---|
দলের প্রত্যেক সদস্যই পর্যায়ক্রমে যাতে বিভিন্ন কাজে অংশগ্রহণ করতে পারে, অবদান রাখতে পারে খুশি। আপা সে বিষয়টি নিশ্চিত করলেন।
তথ্য যাচাই ও বিশ্লেষণ
- খুশি আপা বারবার দলগুলোর কাছ থেকে তথ্যের সঠিকতা যাচাই কীভাবে করবে তার ধারনা নিলেন ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিলেন। তবে দলগুলোর উপর কোন মতামত চাপিয়ে দিলেন না।
- সবাই দলগতভাবে প্রাপ্ত তথ্য যাচাই-বাছাইয়ের মাধ্যমে গ্রহণ-বর্জন করে বিশ্লেষণ করলো এবং নিজেদের কাজের অভিজ্ঞতাসমূহ শ্রেণিকক্ষে সবার সামনে উপস্থাপন করলো।
ফলাফল তৈরি ও উপস্থাপন
- এই পর্যায়ে খুশি আপা জানতে চাইলেন, এই কাজের মধ্য দিয়ে তোমরা মুক্তিযুদ্ধের যেসব ঘটনা খুঁজে এনেছো সেগুলো কীভাবে অন্যদের জানাতে পারো?
- সবাই দলে আলোচনা করে বিভিন্ন সৃজনশীল ও অভিনব উপায় পরিকল্পনা করলো। যেমন- ফটোবুক, ডকুমেন্টারি, দেয়ালিকা, পোস্টার, লিফলেট, ফটোগ্রাফি বা আঁকা ছবি প্রদর্শনী, বই, নাটক ইত্যাদি। খুশি আপা এই ক্ষেত্রে পুরোপুরি স্বাধীনভাবে তাদের পরিকল্পনা করতে দিলেন, শুধু সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ ও ইস্যুসমূহ সম্পর্কে সচেতন করলেন। খুশি আপার পরামর্শ নিয়ে দলগুলো। তাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করলো এবং কোন জাতীয় দিবসে তা অন্যান্য ক্লাসের শিক্ষার্থীদের সাথে শেয়ার করলো ।
- এবার খুশি আপা বললেন, বিদ্যালয়ে উদযাপিত যেকোনো জাতীয় দিবস যেমন, ৭ই মার্চ, ১৭ই মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস, ২৫শে মার্চ গণহত্যা দিবস, ২৬শে মার্চ স্বাধীনতা দিবস, ১৪ই এপ্রিল বা ১লা বৈশাখ বাংলা নববর্ষ, ১৫ই আগস্ট জাতীয় শোক দিবস, ১৪ই ডিসেম্বর শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস, ১৬ই ডিসেম্বর বিজয় দিবস প্রভৃতি জাতীয় দিবসের সাথে মিলিয়ে বিদ্যালয়ে শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও কমিউনিটির ব্যক্তিবর্গের সামনেও তোমাদের প্রাপ্ত ফলাফল উপস্থাপন করতে পারো। আমরা মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক এসব তথ্য পরবর্তী গবেষণার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক বা জাতীয়ভাবে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করবো।
- সংশ্লিষ্ট শিক্ষকগণের প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও ফিডব্যাক অনুসারে নিসর্গ ও অঙ্গেযারে বন্ধুরা তাদের প্রকল্পটি উপস্থাপন অনুষ্ঠানের আয়োজন করলো। অতিথি হিসেবে বিদ্যালয়ের শিক্ষক, থানা শিক্ষা কর্মকর্তা, অভিভাবক, স্থানীয় প্রবীণ ব্যক্তি মুক্তিযোদ্ধারা উপস্থিত থাকলেন।
মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি সংরক্ষণের উদ্যোগ
এরপর খুশি আপা মুক্তিযুদ্ধের এসব স্মৃতি ধরে রাখার স্থায়ী কোন উপায় করা যায় কিনা সে বিষয়ে প্রশ্ন করলেন। বললেন যে, প্রাপ্ত ফলাফলের প্রতিফলন হিসেবে তোমরা নিজ নিজ এলাকায় “শিক্ষার্থী কর্তৃক নির্মিত মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতিস্তম্ভ”/ বিদ্যমান স্মৃতিস্ত/সৌধ আধুনিকায়ন সংরক্ষণ বা পুনঃ নির্মাণের নক্সা তৈরির পরিকল্পনা বা প্রস্তাবনা গ্রহণ করতে পারো এবং এগুলো বাস্তবায়নের জন্য বিদ্যালয় ও স্থানীয় প্রশাসনের (উপজেলা বা জেলা) সহযোগিতার আবেদন করতে পারো। এবার চলো আমরা অধ্যায়ের শেষে সংযুক্ত সতীর্থ মূলায়নের ছক ব্যবহার করে আমাদের দলের সবাই সবার মূল্যায়ন করি।
ডকুমেন্টেশন
সবশেষে দলগুলো দলীয় কাজের বিভিন্ন ধাপের তথ্যসমূহ, আত্ম-প্রতিফলনের লিখিতরূপ এবং অর্জিত শিখনের সারসংক্ষেপ (ছবি/ভিডিও/লিখিতরূপ/ খসড়া এর হার্ড বা সফট কপি) খুশি আপার মাধ্যমে বিদ্যালয়ে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সংরক্ষণ করলো।
৪.১ঃ রুব্রিক্স শিক্ষার্থী কর্তৃক দলের সদস্যদের পারফরমেন্স মূল্যায়ন
Promotion